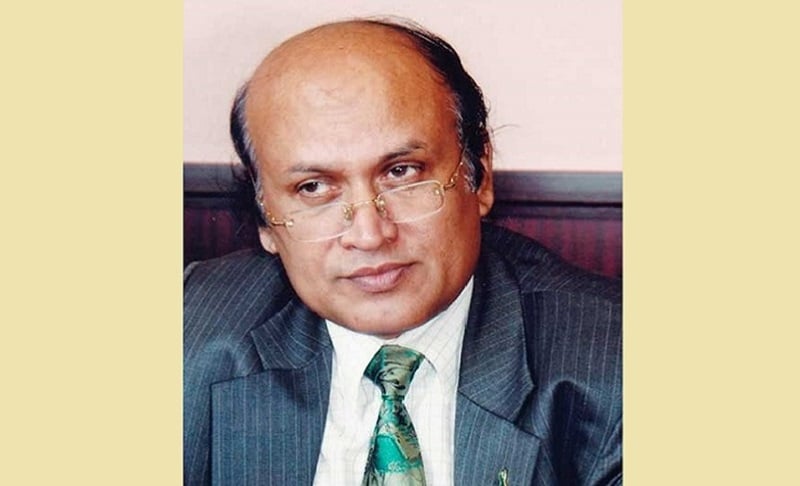ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : ষাটের দশকে ঢাকাই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির দুর্দিনে ইন্ডাস্ট্রিকে চাঙা করতে সেসময় উর্দু ভাষায় সিনেমা নির্মাণে এগিয়ে আসেন এহতেশাম, মুস্তাফিজ, ফজলে দোসানী, আনিস দোসানীর মতো পরিচালকরা।
এরই ধারাবহিকতায় তৈরি হয় ঢাকাইয়া উর্দু সিনেমা ‘চান্দা’, ‘তালাশ’, ‘মালা’, ‘সংগম’, ‘তানহা’, ‘বাহানা’, ‘চকোরী’ ইত্যাদি। পশ্চিম এবং পূর্ব- দুই পাকিস্তানেই উর্দু সিনেমার দোর্দন্ড প্রতাপে বাংলা সিনেমা পতিত হয় এক চরম সংকটে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকাতে ১৪টি বাংলা সিনেমার বিপরীতে তৈরি হয় ১৮টি উর্দু সিনেমা। এই পরিস্থিতিতে বাংলা সিনেমার দর্শককে কীভাবে প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনা যায় সেই চিন্তা নির্মাতা সালাহউদ্দিনের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তখন তিনি নির্মাণ করেন ‘রূপবান’। আর এটিই হয়ে উঠে একটি ইতিহাস।
আবহমান কাল থেকে বাঙালির প্রধান বিনোদন ছিল পুঁথিপাঠ, যাত্রা, পালাগান, কবির লড়াই, গাজন, কীর্তন, ইত্যাদি। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ‘রুপবান’ যাত্রাপালাটির জয়জয়কার ছিল। একদিন এক গ্রামে সারারাত জেগে এ যাত্রাপালাটি দেখেন সালাহউদ্দিন। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, গল্পে ও নাটকীয়তায় মাটির গন্ধ আছে বলেই হয়তো দর্শকের কাছে এর এতো আকর্ষণ।
এছাড়াও এতে আছে হৃদয়গ্রাহী লোক সংগীতের ব্যবহার। এসব চিন্তাভাবনা থেকে এই জনপ্রিয় লোকগাথাটিকে সিনেমার পর্দায় তুলে আনার সিদ্ধান্ত নেন সালাহউদ্দিন। অথচ অন্যদের কাছে তখনো সেটা নিছক যাত্রাপালা যা সিনেমার কোনো বিষয়ই ছিল না। এতে ঝুঁকি বুঝেও তখন নির্মাতা চ‚ড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি ‘রূপবান’ নির্মাণ করবেনই। বিষয়টি নিয়ে তখন অনেকেই আড়ালে হাসাহাসি করেছেন নির্মাতাকে নিয়ে। যাত্রাপালার বিষয় সিনেমা হিসেবে দর্শকের কাছে কতটুকু গ্রহণীয় হবে বিষয়টি নিয়ে অবশ্য সালাহউদ্দিনের মনেও কিছুটা সংশয় ছিল। তবু তিনি সব সংশয় ও উদ্বেগ একপাশে রেখে কিছু টাকা জোগাড় করে ‘রূপবান’ নির্মাণ শুরু করে দেন। যাত্রাপালায় যেসব স্থলে জিনিস ছিল সেসব পরিহার করে পল্লীর সাধারণ মানুষের কাছে যাতে সহজবোধ্য হয় সেই কথা মাথায় রেখে সহজ-সরলভাবে চিত্রনাট্য-সংলাপ লেখা হলো। সিনেমায় যেন লোকজ ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে, লোকজ উপাদানের গন্ধ যাতে কিছুটা হলেও অক্ষুন্ন থাকে সেই চেষ্টাও করা হলো।
পশ্চিম পাকিস্তানে এদেশের লোকগাথাভিত্তিক সিনেমা প্রদর্শনের আকাক্সক্ষায় এটি বাংলা ও উর্দু-দুই ভাষায় তৈরি হয়। শুটিংয়ের সময় একই শট দুইবার নেওয়া হতো। একবার বাংলা সংলাপে, আরেকবার উর্দুতে। সেই অর্থে ‘রূপবান’ই এদেশের প্রথম ডাবল ভার্সন বা দ্বিভাষিক সিনেমা। ১৯৬৫ সালের ৫ নভেম্বর ‘রূপবান’ সিনেমাটি মুক্তি পায়। মুক্তির পর মফস্বলের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ঘটেছিল নানা ঘটনা। নৌকায় কিংবা গরুর গাড়িতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটেছিল কাছাকাছি শহরের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি দেখার জন্য।
১২ বছরের রূপবানের সঙ্গে রাজপুত্র রহিম, যে কিনা সদ্য জন্মলাভ করেছে, তার বিয়ের মাধ্যমে এ কাহিনীর বিস্তৃতি ঘটে। তারপর দৈববাণীর কল্যাণে ১২ দিনের স্বামী রহিমকে নিয়ে ১২ বছরের রূপবানের বনবাস। রূপবানের বনসংগ্রামী জীবন, রহিম বাদশার বেড়ে ওঠা, অপর রাজকন্যা তাজেলের প্রেমে পড়া, পরিশেষে অমোঘ সত্য প্রকাশিত হওয়ার বিষয়াদিই রূপবান লোককাহিনীর উপজীব্য বিষয় ছিল। এর প্রযোজনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। এতে নাম ভ‚মিকায় অভিনয় করেন সুজাতা আজিম। তার পারিবারিক নাম ছিল তন্দ্রা মজুমদার। পরিচালকের কল্যাণে সেটা হয়ে যায় সুজাতা।
মুক্তির পর সিনেমাটির জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে ওঠে যে, নায়িকা সুজাতাকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। অনুরাগীদের ঢল ঠেকানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুলিশ পর্যন্ত মোতায়েন করতে হয়েছে। গ্রামের যেসব মা-চাচীরা ইতিপূর্বে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখার কথা চিন্তাও করেননি, তারাও ‘রূপবান’ দেখতে গরু-মহিষের গাড়িতে করে হলমুখী হয়েছিলেন। এমনকি টিকিট না পেয়ে সারারাত প্রেক্ষাগৃহে থেকে পরের দিন সিনেমা দেখার মতো কান্ডও ঘটেছে। প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা রাতে খিচুড়ি রান্না করে দর্শকদের খাওয়াতেন ও প্রেক্ষাগৃহেই ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সিনেমা আরও ইতিহাস করেছে। এর দৃশ্যে দেখা যায় রূপবান একটি বাঁশে হাত রেখেছিল, যা পরবর্তীতে ষাট টাকায় নিলামে বিক্রি হয়। চলতি বাজারে যার মূল্য এক বা দু আনার বেশি ছিল না। শুধু তাই নয়, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে টানানো রূপবানের ছবি সম্বলিত সিনেমার ব্যানারটি ছিঁড়ে যায়, পরবর্তীতে সেই ছেঁড়া ব্যানারও নিলামে বিক্রি করা হয়।
‘রূপবান’র একসঙ্গে ১৭টি প্রিন্ট প্রকাশ করা হয়। এর আগে প্রিন্ট তৈরি হতো ৪টি অথবা ৫টি। এভাবে রিলিজের আওতা বেড়ে যায়। এতে অনেক চিত্রব্যবসায়ী উৎসাহী হয়ে গ্রাম এলাকায় মৌসুমী সিনেমাহল তৈরি করেন। এভাবে পূর্ব বাংলায় সিনেমার দর্শক কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া রূপবানের সাফল্যে ঢাকার সিনেমা থেকে প্রায় নির্বাসিত বাংলা ভাষা আবার ফিরে আসে। বলা যায়, ঢাকায় বাংলা সিনেমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে।
সালাহ্উদ্দিনের পরিচালনায় পরবর্তীতে ‘রূপবান’ সিনেমাটির উর্দু সংস্করণ মুক্তি পায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬৫ পরবর্তী সময়কে সিনে-সাংবাদিকরা ‘রূপবান যুগ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সিনেমাটিতে সুজাতা ছাড়াও আরও অভিনয় করেন মনসুর, চন্দনা, আনোয়ার হোসেন, ইনাম আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম, তেজেন চক্রবর্তী, তন্দ্রা, রহিমা ও হেলেন। ‘শোনো তাজেল গো’, ‘ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো’, ‘সাগর ক‚লের নাইয়ারে’, ‘মনের দুঃখ কইনারে বন্ধু রাইখাছি অন্তরে’ শিরোনামে রূপবানের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান তখন লোকের মুখে মুখে ছিল। গানগুলোতে কণ্ঠ দেন আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, ইসমত আরা, কুসুম হক, নজমুল হোসেন (শেলী)। গানের কথা লিখেছেন মাসুদ করিম। সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্য সাহা। কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন চিত্রগ্রহণে আবদুস সামাদ, শব্দগ্রহণে মনি বোস ও সম্পাদনায় বশীর হোসেন।
সালাহ উদ্দিন পরিচালিত এ সিনেমাটি পর্দায় আনার পেছনে মূল কারিগর ছিলেন তার সহকারী সফদার আলী ভূঁইয়া ও তার ভাই সিরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া। তাদের দীর্ঘদিনের উৎসাহ উদ্দীপনায় নির্মাতা এটি বানান। এর বাজেট ছিল তৎকালীন দেড় লাখ রুপি। বক্সঅফিসে এটি ব্যাপক আলোড়ন তোলে। এর বাণিজ্যিক সাফল্য অতীতের সকল রেকর্ড ভাঙে। সিনেমার দেশীয়করণে ‘রূপবান’ এর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে একদিকে ভারতীয় সিনেমা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করেন ‘রূপবান’কে। কোন জনপদের নিজস্ব জীবন, ভাষা ও বয়ানরীতির মধ্য থেকে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা এ লোককাহিনী সেই জনপদের পরিচয় ও জীবনচর্চাকে প্রতিফলিত করে। ফলে সেটি যখন চিত্রায়িত হয়, তখন তা জনপদের একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের সিনেমার তেমনই একটি সৃষ্টি ‘রূপবান’।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর